ভারতের কৃষিজ সমাজ ও সংস্কৃতি || কৃষিজ সমাজ ব্যবস্থা্র একটি রূপরেখা
ভারতের কৃষিজ সমাজ ও সংস্কৃতি
আমরা জানি ভারত তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। ভারত কৃষির ওপর নির্ভর করে বিকাশশীল একটি দেশ। ভারতের অধিকাংশ গ্রামগুলি কৃষিভিত্তিক। তবে কৃষি ছাড়াও অন্যান্য প্রাথমিক কার্যাবলির প্রভাব ভারতীয় গ্রামগুলিতে বর্তমান লক্ষণীয়। তাই ভারতের প্রধান ও প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থা কে জানার জন্য আমাদের আগে জানতে হবে ভারতের কৃষিজ সমাজ ও সংস্কৃতি ব্যবস্থাকে। তাই এই বিষয়ে লেখার জন্য কলম ধরেছেন- অমল মন্ডল (মেচেদা, পূর্ব মেদিনীপুর)

♦ কৃষিসমাজ এর ধারণা-
প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে গঠিত কোনও বসতি যখন কৃষি, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস সম্পদ, পশুজ সম্পদ অর্থাৎ জীবনধারণের প্রাথমিক ক্রীয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ও তার ওপর নির্ভরশীল থেকে তখন সেই মনুষ্য বসতিকে গ্রামীণ বসতি বলা হয়। এই ধরণের বসতিকে ভূমি সম্পদ অধিক গুরুত্ব পায়।
ভারতীয় জনগণনা আয়োগের মতে, গ্রাম হল কোনও অনুকুল বা সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত বহু বাসগৃহের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সরল সমারোহ। অন্যভাবে বলা যায় গ্রাম হল একটি সুনিদিষ্ট সীমানা আবদ্ধ ছোট্ট ভূখন্ড, যা সরকারি পরিভাষায় মৌজা নামে পরিচিত।
আবার, কৃষিব্যবস্থা ও কৃষি-সংক্রান্ত কর্মকান্ডের ওপর ভিত্তি করে মানুষের বেঁচে থাকার পরিবেশ, জীবনযাত্রা ও সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে উঠলে তাকে কৃষি সমাজ বা ‘এগ্রিকালচারাল সোসাইটি’ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কৃষিকে কেন্দ্র করে যে সমাজে মানুষ মূল অর্থনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টা পরিচালিত হয় তাকে কৃষিসমাজ বলে।
বিস্তীর্ণ পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চলে সাধারণত কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে।
♦ ভারতের কৃষিসমাজের বৈশিষ্ট-
১. বৃত্তিঃ

ভারতীয় গ্রামীণ বসতির সদস্যরা মুলত কৃষি জীবী। ফলে, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী দের অর্থনৈতিক কার্যাবলিও কৃষি নির্ভর। এই কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি গ্রামীণ জন বসতির জীবনধারা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলিকেও গভীর ভাবে প্রাভাবিত করে। অর্থাৎ ভারতীয় কৃষিজ সমাজ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত।
২. বৃত্তি গত বিন্যাসঃ

কৃষিভিত্তিক সমাজ হলেও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য চাষাবাদের পাশাপাশি পশুপালন, মাছ চাষ, বনজ সম্পদ সংগ্রহ, মধু, মোম ও অন্যান্য সহযোগী পেশা গ্রহণ করে থাকে গ্রামীন মানুষ। বিভিন্ন কারিগর সম্প্রদায় কৃষিভিত্তিক এই সমাজে কৃষিজীবীদের সঙ্গে বসবাস করে, ফলে বিভিন্ন সাংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে।

৩. দারিদ্রঃ

ভারতীয় গ্রামীণ অধিবাসীরা অত্যন্ত গরীব। এদের দৈনিক আয় ও মাথাপিছু আয় কম। এদের খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান অনুন্নত ধরণের। সীমাবদ্ধ কৃষিক্ষেত্রে অনসংখ্যার অধিক চাপের ফলে মাথাপিছু জমি ও ফসল উৎপাদনের পরিমানও খুবই কম। এছাড়া কৃষিজ উৎপাদনের পরিমান কম হওয়ার আরেকটি কারণ গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। যার ফলে কৃষকদের প্রায় ঋণের কবলে পরতে হয়। যার ফলাফল আত্মহত্যা পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

৪. ধীর উন্নয়নঃ
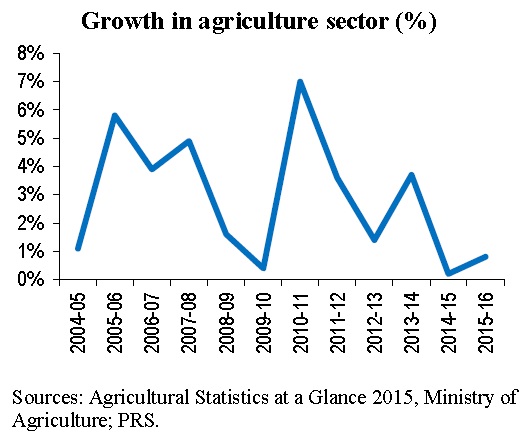
গ্রামীন অর্থনীতি যেহেতু দুর্বল এবং উদ্বৃত্ত সম্পদ বলতে যেহেতু প্রায় কিছুই নাই, তাই গ্রামীন উন্নয়নের হার মন্থর। কৃষিতে উৎপন্ন ফসলের সবটাই গৃহস্থের নিজের প্রযোজনে ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রামীন অর্থনীতি তার চিরাচরিত রূপ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনা। এছাড়াও রয়েছে গ্রাম্য কৃষিসমাজের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় কতৃক নিম্নবিত্তের শোষণ ও অত্যাচার।
৫. রক্ষণশীল সমাজঃ

রক্ষণশীলতা ভারতের গ্রামীণ সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট। সনাতন প্রথা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক কোনও পরিবর্তনই হঠাৎ এরা মেনে নিতে পারেনা।
৬. যৌথ-পরিবার প্রথাঃ

ভারতীয় গ্রামীণ বসতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল যৌথ-পরিবার ব্যবস্থা। পরিবারগুলির অন্নসংস্থানের মূল উৎস কৃষিকাজ হওয়ার ফলেই যৌথ পরিবার ব্যবস্থার প্রযোজনীয়তা দেখা যায়। পরিবারের নারী, পুরুষ, সন্তান-সন্তনি সকলেই যে যার সাধ্যমত চাষ বাসের সঙ্গে যুক্ত কোনও না কোনো কাজে অংশগ্রহন করে। গ্রামাঞ্চলে একান্নবর্তী যৌথ পরিবার এখনও বহুল প্রচলিত।
৭. একাত্মবোধঃ
কৃষিভিত্তিক সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের সমগ্র জীবন যেহেতু সম্পূর্ণভাবে সমাজের মধ্যেই অতিবাহিত হয়, তাই তাদের জীবনযাত্রায় ঐক্য ও সংহতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরণের ‘একাত্মবোধ’ গড়ে ওঠে।
৮. সমষ্টিগত চেতনাঃ

সাংগঠনিক কার্যগত বিচারে প্রতিটি গ্রামীন বসতি এক-একটি সুসংহত একক। গ্রামীন বসতির প্রতিটি সদস্যের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য বোধ থাকে। তারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে চেনে ও জানে। তাদের সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি প্রায় অভিন্ন। গ্রামের উৎসব অনুষ্ঠান বা প্রথা-পার্বণে তারা সমবেত ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি তথা সমষ্টি গত চেতনা লক্ষ করা যায়।
৯. প্রতিবেশীসুলভ আচরণঃ
স্বল্প আয়তনের মধ্যে এক-একটি গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠায় অধিবাসীদের সংখ্যা কম হয়। তাছাড়া প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পুর্ন না হওয়ায় তাদের মধ্যে গভীর প্রতিবেশীসুলভ মানসিকতা তৈরি হয়। অধিবাসীদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ দেখা যায় না, বরং একে অপরের সঙ্গে সহযোগীতা, সহানুভুতি, সমবেদনার সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।
১০. সরলতাঃ
গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা প্রকৃতিগতভাবে সহজ, সরল এবং তাদের আচার-আচরণ স্বতঃফুর্ত। তাদের মধ্যে শঠতা নেই। জীবনধারা সহজ, স্বচ্ছন্দ ও শান্তিপূর্ণ, মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে যন্ত্রণা থাকে না। ফলে সামাজিক অপরাধের ঘটনা বৃহৎভাবে দেখা যায় না। যদিও বা কোনো অপরাধ দেখা দেয় সেটার মোকাবিলা করা হয় মিলেমিশে, যেটা কিন্তু ভারতীয় শহুরে সমাজে খুব বেশি লক্ষ করা যায় না!
১১. ধর্মভাবঃ

ভারতের গ্রামীণ বসতির অধিবাসীরা ধর্মভীরু। আচার, অনুষ্ঠান, পূজার্চনা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষিজীবীরা অধিকমাত্রায় প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। প্রকৃতির আবহাওয়াগত খামখেয়ালকে এরা ভয় ও ভক্তি করে। তবে বর্তমানে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ আধুনিকতার ছোঁইয়া লাগতে শুরু করেছে।
১২. শিক্ষার অভাবঃ

ভারতের গ্রামীন কৃষিভিত্তিক সমাজে শিক্ষার হার খুব কম। দারিদ্র ও শহরের থেকে স্থানিক দুরত্বও উচ্চশিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণেও কৃষির অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। যার ফলাফল ব্যক্তি তথা দেশের ওপর পত্যক্ষ প্রভাব পরে চলেছে।
১৩. স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাঃ

পূর্বে ভারতবর্ষের গ্রামীন বসতিগুলি সাবেকি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তথা নিজস্ব স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারা পরিচালিত হত। বর্তমানে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় গ্রামীণ প্রশাসনের প্রতিনিধি নির্বাচন অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক ও সংবিধান সম্মত এবং শাসন বিধিও আইনানুগ হয়েছে।
— সমাপ্ত—
স্টুডেন্টস কেয়ার দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত – অফলাইন বা অনলাইন প্রকাশনার জন্য স্টুডেন্টস কেয়ারের লিঙ্ক সহ সূত্র দেওয়া আবশ্যক।
আপনারাও আপনাদের মূল্যবান লেখা আমাদের পাঠিয়ে দিতে পারেন। লেখা পাঠানোর জন্য আমাদের নীতিমালাটি পড়ে আমাদের ইমেল ([email protected]) মারফৎ পাঠান।


